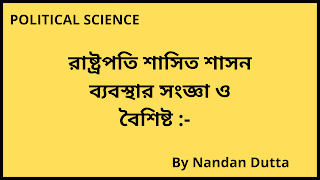রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য / তুলনামূলক আলোচনা।
রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য / তুলনামূলক আলোচনা।
Distinction / Difference between Parliamentary and Presidential forms of Government . ( In Bengali )
রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য।
রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য।
ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যথা - রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার ও মন্ত্রিসভা পরিচালিত বা সংসদীয় সরকার। এই দুই ধরণের শাসন ব্যবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তবে , উভয় ধরণের সরকারের ক্ষেত্রে বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ :-
১. আইনসভার গঠনগত ক্ষেত্রে পার্থক্য :- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত হন না। তিনি সরাসরি জনগণ কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাই রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান কোনোভাবেই আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না বা আইনসভা রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না।
কিন্তু সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান হন নিয়মতান্ত্রিক এবং তিনি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হন। তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন। এমনকি রষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত কোনো বিল আইনে পরিণত হতে পারেনা।
২. রাষ্ট্রপ্রধানের প্রকৃতিগত ক্ষেত্রে পার্থক্য :- রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যাস্ত থাকে। তিনি হলেন দেশের প্রকৃত শাসক।
অন্যদিকে মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান হলেন নিয়মতান্ত্রিক। অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে তিনি রাষ্ট্রের প্রধান হলেও সরকারের প্রধান নন। অর্থাৎ তিনি তাঁর অধীনস্থ মন্ত্রীবর্গ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রধান হন প্রধানমন্ত্রী।
৩. আইনসভার নিকট দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে পার্থক্য :- রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণ কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাই তিনি তার কাজের জন্য কোনোভাবেই আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নন।
কিন্তু মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারে মন্ত্রিসভা আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত হয়। ফলে তারা জনগণ ও আইনসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে।
৪. রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির ক্ষেত্রে পার্থক্য :- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে আইনসভা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেনা। কেবলমাত্র অক্ষমতা , দেশদ্রোহীতা - ইত্যাদি অভিযোগের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়।
কিন্তু সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাকে আইনসভাকে সর্বদা সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় রাখতে হয়। মন্ত্রিপরিষদ সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারালে কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে পারে আইনসভা।
৫. আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পার্থক্য :- রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি স্বীকৃত থাকে বলে আইনসভা ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে কোনোরূপ সম্পর্ক থাকেনা। এখানে আইনসভা কোনোভাবেই রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা এবং রাষ্ট্রপতি আইনসভার অধিবেশনে অংশগ্রহণ বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।
কিন্তু সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকার ও আইনসভার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক থাকে। আইনসভা এখানে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকেই মন্ত্রিসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন।
৬. মন্ত্রিসভার ক্ষমতাগত ক্ষেত্রে পার্থক্য :- রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ নির্বাচিত হন সরাসরি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক। মন্ত্রীদের কার্যকালের স্থায়িত্ব নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা - অনিচ্ছার উপর। এখানে মন্ত্রীবর্গ রাষ্ট্রপতির অনুগত কর্মচারীমাত্র।
কিন্তু মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীরাই প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। এই ধরণের শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকলেও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের স্বাধীন ক্ষমতা ও নীতি প্রণয়নের অধিকার থাকে।
৭. মন্ত্রিসভার গঠনগত ক্ষেত্রে পার্থক্য :- রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ সরাসরি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছা - অনিচ্ছার ভিত্তিতে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী বা অন্যান্যদেরকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।
কিন্তু মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের সদস্যদের নিয়োগ করলেও তিনি তা করেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতে। অর্থাৎ ক্যাবিনেট গঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সরাসরি কোনো ক্ষমতাভোগ করেন না।
৮. স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে পার্থক্য :- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার চেয়ে অধিক স্থায়ী হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া রাষ্ট্রপতি বা অন্যান্য মন্ত্রীদের পদচ্যুত করা যায়না।
কিন্তু মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো যেতে পারে।
৯. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য :- রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হয়। এখানে শাসন , আইন ও বিচার বিভাগ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে পরস্পর পরস্পরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কার্যপরিচালনা করে।
কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হয়না। ফলে এখানে আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে এবং কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পরস্পরকে প্রভাবিত করে।
১০. বিচার বিভাগের প্রাধান্যের ক্ষেত্রে :- রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের প্রাধান্য অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে।
কিন্তু মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তে আইনসভাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং আইন ও শাসন বিভাগ বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
১১. জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্য :- রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে সংসদীয় ব্যবস্থার তুলনায় অধিক কার্যকরী। এখানে রাষ্ট্রপতি নিজেই জরুরি অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।
কিন্তু মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের আলাপ - আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তাই জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা অধিক কার্যকরী নয়।
১২. আইনসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতার ক্ষেত্রে পার্থক্য :- রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণ কর্তৃক নিযুক্ত হন। এখানে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের সাথে আইন সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতার কোনো সম্পর্ক নেই।
কিন্তু মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় সরকার গঠিত হয় আইন সভাতে সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। একমাত্র সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার গঠন করা যায়না।